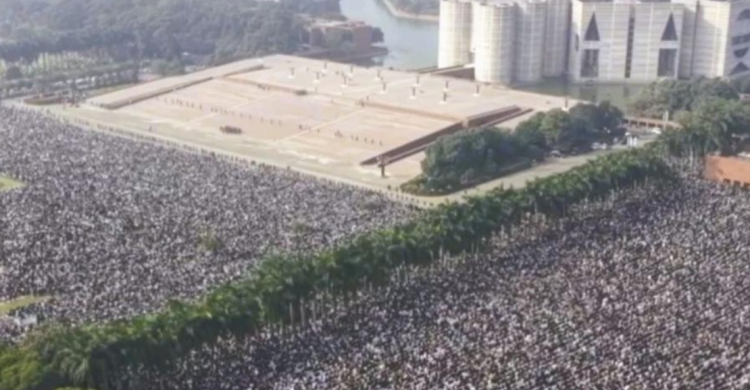বিপন্ন বেদেদের বেদনাগাথা

নাগরিক প্রতিবেদন
২১ মে, ২০২৪, 9:01 PM

বিপন্ন বেদেদের বেদনাগাথা
‘সিঙা লাগাই, দাঁতের পোকা ফালাই’- বাংলার জনপদে কাঁধে ঝোলা, কোমরে আঁচল প্যাঁচানো, হাতে কাচের চুড়ি পরা একশ্রেণির নারীর কণ্ঠে সুর করে বলা এ কথাগুলো শোনা যেত বহুকাল ধরে। বর্তমানে তেমন একটা দেখা যায় না তাদের, সেই সুরও আর সচরাচর কানে বাজে না। ‘বাইদানি’ নামে পরিচিত এই নারীরা বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত। বেদেরা বাংলাদেশের একমাত্র যাযাবর শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠী। ঐতিহ্যগতভাবে ভূমিহীন এ মানুষরা দলবদ্ধভাবে নদীতে বসবাস করে। নৌকায় ঘুরে ঘুরেই জীবনসংগ্রাম চলে তাদের। তাই তারা ‘জল যাযাবর’ বা ‘নদী যাযাবর’ নামেও পরিচিত। আগে নদীনালা, খালবিলে দেখা যেত এদের নৌকার বহর। এসব বহর ‘বেদের বহর’ নামেই পরিচিত ছিল। বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন ‘বাদিয়া’, ‘বাইদ্যা’ বা ‘বইদ্যানি’ নামেও পরিচিত। এ নামগুলোর উৎপত্তি বৈদ্য (চিকিৎসক) থেকে।
প্রাচীনকাল থেকেই বেদেরা কবিরাজি, ঝাঁড়ফুঁকসহ বিভিন্ন ভেষজ চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত। অনেকে অবশ্য দাবি করেন, বেদে শব্দটির উৎপত্তি বেদুইন থেকে।
কথিত আছে, ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ বল্লার রাজার সঙ্গে প্রথম ঢাকায় আগমন ঘটে বেদেদের। প্রথমে তারা ঢাকার অদূরে বিক্রমপুরে আস্তানা গাড়ে। পরে জীবিকার খোঁজে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আটটি গোত্রে বিভক্ত এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালবেদে, সাপুড়িয়া, বাজিকর, সান্দার, টোলা, মিরশিকারি, বারিয়াল সান্দা ও গাইন বেদে প্রধান। তাদের আদি পেশা হলো কবিরাজি ও ভেষজ ওষুধ বিক্রি করা। এ ছাড়া সাপ খেলা, সাপের কামড়ের চিকিৎসা, সাপ বিক্রি, তাবিজ বিক্রি, ঝাঁড়ফুঁক, শিঙা লাগানো (কাপিং থেরাপি), ব্যথা দূর করতে গরুর শিং দিয়ে রক্ত টেনে আনা, দাঁতের চিকিৎসা, বানর খেলা, জাদু দেখানো- এসব কাজ করে থাকে তারা। আগের দিনের মানুষ বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কাছে এসব পদ্ধতির চাহিদা ছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও বিকাশের ফলে সচেতন হয়ে উঠছে মানুষ। এতে বিশ্বাস কমেছে প্রাচীন পদ্ধতিতে, একইসঙ্গে কমেছে ওঝা-বৈদ্য-নির্ভরতা। স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে এ পেশার মানুষদের জীবিকার সংকট। তাই এখন আর গ্রামগঞ্জেও আগের মতো দেখা যায় না শিঙা লাগানো বা ঝাঁড়ফুঁকের দৃশ্য। তবে বর্তমানে শহরে রাস্তাঘাটে মাঝেমধ্যেই বেদে সম্প্রদায়ের নারীদের সাপের ভয় দেখিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে টাকা তুলতে দেখা যায়।
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে জীবিকার তাগিদে বেদে সম্প্রদায়ের অনেকেই বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে নতুন পেশা খুঁজে নিচ্ছেন। টঙ্গীর তুরাগ নদের পাড়ে বেদে পল্লিতে খাদিজা নামের এক নারীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিনি এবং তার স্বামী আগে সাপের খেলা দেখাতেন। কিন্তু এখন তারা কেউই এ পেশায় নেই। কারণ জানতে চাইলে বলেন, ‘এই কামে এহন আর আগের মতো আয় হয় না। শহরে সবাই ঘরে সময় কাটায় বেশি, খেলা দেহানের মতো খোলামেলা পরিবেশও নাই।’
রবিউল নামের এক তরুণ বলেন, এ পেশার প্রতি আমাদের সম্প্রদায়ের তরুণাই আগ্রহ হারাচ্ছে বেশি। আমার বন্ধুরা অনেকেই বিভিন্ন ব্যবসা করছে। আমি নিজেও ব্যবসা করি। তাতে আয় কম হলেও আদি পেশা থেকে অনেক ভালো আছি। স্বেচ্ছায় কেউ বাপ-দাদার পেশা ছাড়তে চায় না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা নিরুপায়।
আবার অনেকে জানান, আগের পেশা পরিবর্তনের অন্যতম কারণ সাপ কমে যাওয়া। মাঝেমধ্যে দুই-চারটা খুঁজে পাওয়া গেলেও তা বন বিভাগের সংরক্ষণে চলে যায়। বিরল প্রজাতির তো বটেই, সাধারণ প্রজাতির সাপও মেলে না।
তবে অতীতে বেদেদের জীবনধারা এমন ছিল না। বহুকাল ধরে লোকালয়ের পার্শ্ববর্তী নদীবন্দর কিংবা তীরঘেঁষে ছোট ছোট নৌকার বহর নিয়ে দলবেঁধে বসবাস করত তারা। যাযাবর এ সম্প্রদায়কে নিয়ে তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র, লেখা হয়েছে গান ও বই। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশের নদীগুলো সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংকট বেড়েছে বেদেদের জীবিকার।
একসময় জীবিকার তাগিদেই নদীতীরবর্তী এলাকায় আসা শুরু করে তারা। বহু বেদে পরিবার এখন গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে বসবাস শুরু করেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। ঢাকার সাভার, মুন্সীগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গাজীপুরের জয়দেবপুর, চট্টগ্রামের হাটহাজারী, মিরেরসরাই, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় তাদের বসবাস দেখা যায়। তবে এভাবে বসবাসেও বিপন্ন হচ্ছে তাদের জীবন। নিরাপদ মাথা গোঁজার ঠাঁই, সন্তানদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসার কোনো নিশ্চয়তা নেই তাদের। শত ছিন্ন পলিথিন কিংবা সিমেন্টের ব্যাগের ছাউনি দেওয়া সম্পূর্ণ অস্থায়ী কুঁড়েঘরে ঠিকানাবিহীন জীবন বেদেদের। যা আয় হয়, তা দিয়ে কোনোমতে দিন কাটে তাদের। কঠিন রোগ হলেও চিকিৎসা জোটে না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করানোর ইচ্ছা থাকলেও পরিবেশ ও অর্থাভাবে তা সম্ভব হয় না। এভাবেই দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার বেদে সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।
নাগরিক প্রতিবেদন
২১ মে, ২০২৪, 9:01 PM

‘সিঙা লাগাই, দাঁতের পোকা ফালাই’- বাংলার জনপদে কাঁধে ঝোলা, কোমরে আঁচল প্যাঁচানো, হাতে কাচের চুড়ি পরা একশ্রেণির নারীর কণ্ঠে সুর করে বলা এ কথাগুলো শোনা যেত বহুকাল ধরে। বর্তমানে তেমন একটা দেখা যায় না তাদের, সেই সুরও আর সচরাচর কানে বাজে না। ‘বাইদানি’ নামে পরিচিত এই নারীরা বেদে সম্প্রদায়ভুক্ত। বেদেরা বাংলাদেশের একমাত্র যাযাবর শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠী। ঐতিহ্যগতভাবে ভূমিহীন এ মানুষরা দলবদ্ধভাবে নদীতে বসবাস করে। নৌকায় ঘুরে ঘুরেই জীবনসংগ্রাম চলে তাদের। তাই তারা ‘জল যাযাবর’ বা ‘নদী যাযাবর’ নামেও পরিচিত। আগে নদীনালা, খালবিলে দেখা যেত এদের নৌকার বহর। এসব বহর ‘বেদের বহর’ নামেই পরিচিত ছিল। বেদে সম্প্রদায়ের লোকজন ‘বাদিয়া’, ‘বাইদ্যা’ বা ‘বইদ্যানি’ নামেও পরিচিত। এ নামগুলোর উৎপত্তি বৈদ্য (চিকিৎসক) থেকে।
প্রাচীনকাল থেকেই বেদেরা কবিরাজি, ঝাঁড়ফুঁকসহ বিভিন্ন ভেষজ চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত। অনেকে অবশ্য দাবি করেন, বেদে শব্দটির উৎপত্তি বেদুইন থেকে।
কথিত আছে, ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ বল্লার রাজার সঙ্গে প্রথম ঢাকায় আগমন ঘটে বেদেদের। প্রথমে তারা ঢাকার অদূরে বিক্রমপুরে আস্তানা গাড়ে। পরে জীবিকার খোঁজে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আটটি গোত্রে বিভক্ত এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালবেদে, সাপুড়িয়া, বাজিকর, সান্দার, টোলা, মিরশিকারি, বারিয়াল সান্দা ও গাইন বেদে প্রধান। তাদের আদি পেশা হলো কবিরাজি ও ভেষজ ওষুধ বিক্রি করা। এ ছাড়া সাপ খেলা, সাপের কামড়ের চিকিৎসা, সাপ বিক্রি, তাবিজ বিক্রি, ঝাঁড়ফুঁক, শিঙা লাগানো (কাপিং থেরাপি), ব্যথা দূর করতে গরুর শিং দিয়ে রক্ত টেনে আনা, দাঁতের চিকিৎসা, বানর খেলা, জাদু দেখানো- এসব কাজ করে থাকে তারা। আগের দিনের মানুষ বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কাছে এসব পদ্ধতির চাহিদা ছিল। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও বিকাশের ফলে সচেতন হয়ে উঠছে মানুষ। এতে বিশ্বাস কমেছে প্রাচীন পদ্ধতিতে, একইসঙ্গে কমেছে ওঝা-বৈদ্য-নির্ভরতা। স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে এ পেশার মানুষদের জীবিকার সংকট। তাই এখন আর গ্রামগঞ্জেও আগের মতো দেখা যায় না শিঙা লাগানো বা ঝাঁড়ফুঁকের দৃশ্য। তবে বর্তমানে শহরে রাস্তাঘাটে মাঝেমধ্যেই বেদে সম্প্রদায়ের নারীদের সাপের ভয় দেখিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে টাকা তুলতে দেখা যায়।
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে জীবিকার তাগিদে বেদে সম্প্রদায়ের অনেকেই বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে নতুন পেশা খুঁজে নিচ্ছেন। টঙ্গীর তুরাগ নদের পাড়ে বেদে পল্লিতে খাদিজা নামের এক নারীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিনি এবং তার স্বামী আগে সাপের খেলা দেখাতেন। কিন্তু এখন তারা কেউই এ পেশায় নেই। কারণ জানতে চাইলে বলেন, ‘এই কামে এহন আর আগের মতো আয় হয় না। শহরে সবাই ঘরে সময় কাটায় বেশি, খেলা দেহানের মতো খোলামেলা পরিবেশও নাই।’
রবিউল নামের এক তরুণ বলেন, এ পেশার প্রতি আমাদের সম্প্রদায়ের তরুণাই আগ্রহ হারাচ্ছে বেশি। আমার বন্ধুরা অনেকেই বিভিন্ন ব্যবসা করছে। আমি নিজেও ব্যবসা করি। তাতে আয় কম হলেও আদি পেশা থেকে অনেক ভালো আছি। স্বেচ্ছায় কেউ বাপ-দাদার পেশা ছাড়তে চায় না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা নিরুপায়।
আবার অনেকে জানান, আগের পেশা পরিবর্তনের অন্যতম কারণ সাপ কমে যাওয়া। মাঝেমধ্যে দুই-চারটা খুঁজে পাওয়া গেলেও তা বন বিভাগের সংরক্ষণে চলে যায়। বিরল প্রজাতির তো বটেই, সাধারণ প্রজাতির সাপও মেলে না।
তবে অতীতে বেদেদের জীবনধারা এমন ছিল না। বহুকাল ধরে লোকালয়ের পার্শ্ববর্তী নদীবন্দর কিংবা তীরঘেঁষে ছোট ছোট নৌকার বহর নিয়ে দলবেঁধে বসবাস করত তারা। যাযাবর এ সম্প্রদায়কে নিয়ে তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র, লেখা হয়েছে গান ও বই। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশের নদীগুলো সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংকট বেড়েছে বেদেদের জীবিকার।
একসময় জীবিকার তাগিদেই নদীতীরবর্তী এলাকায় আসা শুরু করে তারা। বহু বেদে পরিবার এখন গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে বসবাস শুরু করেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। ঢাকার সাভার, মুন্সীগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, গাজীপুরের জয়দেবপুর, চট্টগ্রামের হাটহাজারী, মিরেরসরাই, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় তাদের বসবাস দেখা যায়। তবে এভাবে বসবাসেও বিপন্ন হচ্ছে তাদের জীবন। নিরাপদ মাথা গোঁজার ঠাঁই, সন্তানদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও চিকিৎসার কোনো নিশ্চয়তা নেই তাদের। শত ছিন্ন পলিথিন কিংবা সিমেন্টের ব্যাগের ছাউনি দেওয়া সম্পূর্ণ অস্থায়ী কুঁড়েঘরে ঠিকানাবিহীন জীবন বেদেদের। যা আয় হয়, তা দিয়ে কোনোমতে দিন কাটে তাদের। কঠিন রোগ হলেও চিকিৎসা জোটে না। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করানোর ইচ্ছা থাকলেও পরিবেশ ও অর্থাভাবে তা সম্ভব হয় না। এভাবেই দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার বেদে সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।