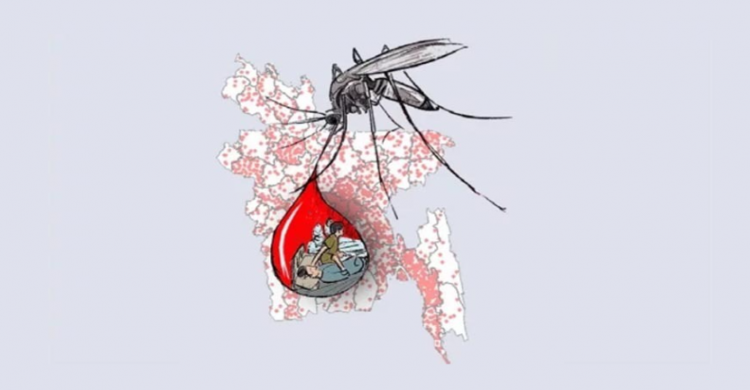তিন দশকে বেড়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, বাড়েনি সেবার মান

নাগরিক প্রতিবেদন
১২ মার্চ, ২০২৪, 3:55 PM

তিন দশকে বেড়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, বাড়েনি সেবার মান
দেশে গত তিন দশকে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ। তবে চিকিৎসা পরিসর বা অবকাঠামো বাড়লেও সে তুলনায় সেবার মান বাড়েনি। এমনকি মান নিশ্চিতের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্রেডিটেশনের বিষয়েও এসব প্রতিষ্ঠানের বেশ অনাগ্রহ। এ কারণেই দেশের স্বাস্থ্যসেবা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায় না বলে মনে করছেন জনস্বাস্থ্যবিদরা।
আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যোগ্যতার একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হচ্ছে অ্যাক্রেডিটেশন। যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট কমিশন ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই), কলেজ অব আমেরিকান প্যাথলজিস্ট (সিএপি), যুক্তরাজ্যের ইউনাইটেড কিংডম অ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (ইউকেএএফ), ভারতের ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর হসপিটাল অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রভাইডার (এনএবিএইচ), অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল অন হেলথকেয়ার স্ট্যান্ডার্ডসসহ (এসিএইচএস) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশ কয়েকটি সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে এ স্বীকৃতি দেয়। কোনো কোনোটি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন দেয় আবার কোনোটি দেয় পুরো হাসপাতালের স্বীকৃতি। তবে অ্যাক্রেডিটেশন না থাকার কারণে কয়েকটি ছাড়া দেশের প্রায় সব হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে কোনো বিদেশী চিকিৎসা নিলে স্বাস্থ্যবীমা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়।
দেশে অ্যাক্রেডিটেশন নিয়ে কাজ করে কেবল শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)। সরকারের সংস্থাটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকেও অ্যাক্রেডিটেশন দেয়। বিএবির তথ্য বলছে, দেশে এ পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জের সাতটি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে তারা অ্যাক্রেডিটেশন দিয়েছে। তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান হাসপাতালকে অ্যাক্রেডিটেশন দিলে তাতে কখনই সঠিক মান নিশ্চিত হবে না। কেননা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে বৈশ্বিক স্বীকৃতি দিতে বিএবির কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয়। এমনকি তাদের সত্যায়ন আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যও হয় না।
রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের শীর্ষ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, হাসপাতাল বা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাগুলোর মান ঠিক রয়েছে কিনা বা যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করাই অ্যাক্রেডিটেশন। এর জন্য জেসিআই বিশ্ব স্বীকৃত। মার্কিন সংস্থাটি পুরো হাসপাতালকেই অ্যাক্রেডিট করে আর সিএপির মতো সংস্থা পরীক্ষার অ্যাক্রেডিট করে। এরা মূলত কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট, পেশেন্ট সেফটি ও পলিসিগুলো দেখে। প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে। সেক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যে বোর্ড রয়েছে তা বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নয়।
বেশকিছু শর্ত ও নিয়ম মেনেই বিএবি অ্যাক্রেডিটেশন দেয় বলে জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক মু. আনোয়ারুল আলম। তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্যসেবার বিষয়গুলো বেশ সংবেদনশীল। প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আসতে বহু শর্ত মানতে হয়। ২০০৬ সালের একটি আইনের মাধ্যমে আমাদের অ্যাক্রেডিটেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেসব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে আবেদন করছে তাদের আমরা যাচাই-বাছাই শেষে স্বীকৃতি দিচ্ছি। এছাড়া অন্যদেরও অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে সরকারের একটি উদ্যোগ রয়েছে।’
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য প্রশাসন, ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স, ক্লিনিক্যাল রিসার্চ, অর্থনীতি, কূটনীতি, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা জেমস লিন্ড ইনস্টিটিউট। সংস্থাটি বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা পর্যটন, বীমা, করপোরেট প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন বাজার শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার মানের চাহিদাও বেড়েছে। ফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান নিশ্চয়তার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। হাসপাতালের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য এটি অন্যতম উপকরণ, যা সেবার মান নিশ্চিতেও কাজ করে।
স্বাস্থ্যসেবার জন্য অ্যাক্রেডিটেশন গুরুত্বপূর্ণ হলেও দেশে আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানই এর জন্য আগ্রহী হয় না। কেননা এতে অনেক খরচ করতে হয়। দেশের নামিদামি বেসরকারি একটি হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, তার প্রতিষ্ঠান জেসিআইতে আবেদন করতে চেয়েছিল। তবে তারা অনেক বেশি ফি চাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। অ্যাক্রেডিটেশন মূলত একটি বাণিজ্যিক পণ্য। সাধারণত জেসিআইয়ের মতো সংস্থার প্রি-অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য ৪০ লাখ টাকা ফি দিতে হয়। এরপর তারা ট্রেনিং দেয়, ডকুমেন্টেশন করে। পরে একটি মক অডিট হয়। এতেও অনেক ফি দিতে হয়। এরপর মূল অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য ৫০ হাজার ডলার দিতে হয়। তিন বছর অন্তর দিতে হয় আরো ৫০ হাজার ডলার করে। তবে অ্যাক্রেডিটেশন না থাকলে বিদেশী রোগীরা চিকিৎসাসেবা নিতে আগ্রহী হন না। কেননা চিকিৎসার পর বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর কাগজপত্র তাদের দেশের স্বাস্থ্যবীমা প্রতিষ্ঠানগুলো আমলে নিতে চায় না। এতে তাদের বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়।
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে সরকারির তুলনায় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার পরিসর বড়। সারা দেশে সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ৬৪০ (ইউনিয়ন পর্যায় বাদে)। আর অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে ৫ হাজার ৩০টি, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ১০ হাজারের বেশি এবং ব্লাড ব্যাংক ১৯২টি।
দেশে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কেবল ১০টির মতো বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অ্যাক্রেডিটেশন রয়েছে। এ তথ্য জানিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক তিন কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, ‘প্রায় দেড় দশক আগে অ্যাক্রেডিটেশনের ওপর সরকার গুরুত্ব দেয়। বিষয়টি নিয়ে মূলত কাজ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল পরিচালক। তবে যারাই দায়িত্বে ছিলেন তারা এটিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। আবার কোনো বেসরকারি হাসপাতাল বা রোগ নির্ণয় প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনতে গেলে কিছু রাজনৈতিক চাপও থাকে। এক হাসপাতাল গ্রেড ‘এ’ আর অন্য হাসপাতাল গ্রেড ‘সি’ করলে চাপে পড়তে হয়।’
ওই কর্মকর্তারা আরো জানান, হাসপাতাল বা রোগ নির্ণয় প্রতিষ্ঠানের মান নিশ্চিতের দিক দিয়ে অন্তত ৫০০টি শর্ত ও নির্দেশনা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) অনেক নির্দেশনা আছে। জেসিআইয়ের অ্যাক্রেডিটেশনের বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী হাসপাতালগুলোকে তারকা চিহ্নিত করতে হয়। এতে ব্যয়ও অনেক বেশি। দেশে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অবকাঠামো নেই, লোকবল নেই। একই সঙ্গে অ্যাক্রেডিটেশনের আবহ তৈরি হয়নি।
রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) সাবেক পরিচালক ডা. আবু মোহাম্মদ জাকির হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, ‘সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই আস্থার সংকট রয়েছে। এক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন প্রয়োজন। এর মূল লক্ষ্য হলো চিকিৎসাসেবার সব মান নিশ্চিত করা। প্রতিটি পরীক্ষা, হাসপাতাল বা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের অবকাঠামো, জনবলের দক্ষতা থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয় নিখুঁতভাবে দেখা হয়।’
দেশের প্রথম সারির কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের জেসিআই, সিএপি, এনএবিএইচের অ্যাক্রেডিটেশন রয়েছে। এর মধ্যে ল্যাবএইড হাসপাতাল কয়েক বছর আগে এনএবিএইচ ও সিএপির অ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করেছে। এ বিষয়ে ল্যাবএইড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এএম শামীম বণিক বার্তাকে বলেন, ‘ভারতের এনএবিএইচ ও যুক্তরাষ্ট্রের সিএপির অ্যাক্রেডিটেশন আমাদের হাসপাতালের রয়েছে। এর মধ্যে প্যাথলজির জন্য রয়েছে সিএপি ও হাসপাতালের জন্য এনএবিএইচ অ্যাক্রেডিটেশন। হাসপাতালকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এ স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ। এটা না থাকলে বিদেশীরা বাংলাদেশে চিকিৎসা নিতে আগ্রহী হন না। ভারতে এমন নিয়ম আছে যে হাসপাতাল চালুর পর অ্যাক্রেডিটেশন নিতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক। তারা দুই বছর পরপর অ্যাক্রেডিটেশন নবায়ন করে।’
জেসিআইয়ের অ্যাক্রেডিটেশন রয়েছে এভারকেয়ার হাসপাতালেরও। এ বিষয়ে হাসপাতালটির বাংলাদেশ পরিচালক (মেডিকেল সার্ভিসেস) ডা. আরিফ মাহমুদ বণিক বার্তাকে বলেন, ‘আমাদের হাসপাতাল যখন প্রতিষ্ঠা পায় তখনই প্রচেষ্টা ছিল যেন আন্তর্জাতিক মানের সেবা দেয়া যায়। ২০০৮ সালে আমরা জেসিআইয়ের অ্যাক্রেডিটেশন লাভ করি। এ পর্যন্ত ছয়বার অডিট হয়েছে। দেশ থেকে বহু মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নিতে যান। তারা ভালো মানের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে চান। অ্যাক্রেডিটেশন সে মানের নিশ্চয়তা দেয়। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জেসিআই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সংস্থা।’
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২২ সালে ‘হেলথ কেয়ার অ্যাক্রেডিটেশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কেয়ার’ শিরোনামে এক প্রকাশনায় উল্লেখ করে, অ্যাক্রেডিটেশন বা স্বীকৃতি মূলত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা ও মান পর্যালোচনা করে। এ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রমাণভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা, যথাযোগ্য সেবা, মানের স্তর, ক্লিনিক্যাল ও সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো পর্যালোচনা করা হয়।
অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য যেসব বিষয় মানা প্রয়োজন তা দেশের বেশির ভাগ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নেই বলে মন্তব্য করেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন ও রেফারেল সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শাহেদ আলী জিন্নাহ। তার মতে, দেশের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা নিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি কম। আর অ্যাক্রেডিটেশন পেতে হলে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে হবে। এতে ব্যয়ও করতে হয় প্রচুর।
সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, ‘অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আইন হয়েছে। এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। হাসপাতালগুলোর যেন অ্যাক্রেডিটেশন থাকে তার জন্য সরকার কাজ করছে।’
নাগরিক প্রতিবেদন
১২ মার্চ, ২০২৪, 3:55 PM

দেশে গত তিন দশকে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ। তবে চিকিৎসা পরিসর বা অবকাঠামো বাড়লেও সে তুলনায় সেবার মান বাড়েনি। এমনকি মান নিশ্চিতের জন্য অতিগুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্রেডিটেশনের বিষয়েও এসব প্রতিষ্ঠানের বেশ অনাগ্রহ। এ কারণেই দেশের স্বাস্থ্যসেবা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায় না বলে মনে করছেন জনস্বাস্থ্যবিদরা।
আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যোগ্যতার একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হচ্ছে অ্যাক্রেডিটেশন। যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট কমিশন ইন্টারন্যাশনাল (জেসিআই), কলেজ অব আমেরিকান প্যাথলজিস্ট (সিএপি), যুক্তরাজ্যের ইউনাইটেড কিংডম অ্যাক্রেডিটেশন ফোরাম (ইউকেএএফ), ভারতের ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর হসপিটাল অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রভাইডার (এনএবিএইচ), অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল অন হেলথকেয়ার স্ট্যান্ডার্ডসসহ (এসিএইচএস) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশ কয়েকটি সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে এ স্বীকৃতি দেয়। কোনো কোনোটি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন দেয় আবার কোনোটি দেয় পুরো হাসপাতালের স্বীকৃতি। তবে অ্যাক্রেডিটেশন না থাকার কারণে কয়েকটি ছাড়া দেশের প্রায় সব হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে কোনো বিদেশী চিকিৎসা নিলে স্বাস্থ্যবীমা পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়।
দেশে অ্যাক্রেডিটেশন নিয়ে কাজ করে কেবল শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)। সরকারের সংস্থাটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকেও অ্যাক্রেডিটেশন দেয়। বিএবির তথ্য বলছে, দেশে এ পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিরাজগঞ্জের সাতটি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে তারা অ্যাক্রেডিটেশন দিয়েছে। তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান হাসপাতালকে অ্যাক্রেডিটেশন দিলে তাতে কখনই সঠিক মান নিশ্চিত হবে না। কেননা স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে বৈশ্বিক স্বীকৃতি দিতে বিএবির কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয়। এমনকি তাদের সত্যায়ন আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যও হয় না।
রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের শীর্ষ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, হাসপাতাল বা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাগুলোর মান ঠিক রয়েছে কিনা বা যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করাই অ্যাক্রেডিটেশন। এর জন্য জেসিআই বিশ্ব স্বীকৃত। মার্কিন সংস্থাটি পুরো হাসপাতালকেই অ্যাক্রেডিট করে আর সিএপির মতো সংস্থা পরীক্ষার অ্যাক্রেডিট করে। এরা মূলত কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট, পেশেন্ট সেফটি ও পলিসিগুলো দেখে। প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে। সেক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যে বোর্ড রয়েছে তা বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নয়।
বেশকিছু শর্ত ও নিয়ম মেনেই বিএবি অ্যাক্রেডিটেশন দেয় বলে জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক মু. আনোয়ারুল আলম। তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্যসেবার বিষয়গুলো বেশ সংবেদনশীল। প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আসতে বহু শর্ত মানতে হয়। ২০০৬ সালের একটি আইনের মাধ্যমে আমাদের অ্যাক্রেডিটেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেসব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান স্ব-উদ্যোগে আবেদন করছে তাদের আমরা যাচাই-বাছাই শেষে স্বীকৃতি দিচ্ছি। এছাড়া অন্যদেরও অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়নে সরকারের একটি উদ্যোগ রয়েছে।’
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য প্রশাসন, ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স, ক্লিনিক্যাল রিসার্চ, অর্থনীতি, কূটনীতি, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা জেমস লিন্ড ইনস্টিটিউট। সংস্থাটি বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা পর্যটন, বীমা, করপোরেট প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন বাজার শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার মানের চাহিদাও বেড়েছে। ফলে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান নিশ্চয়তার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। হাসপাতালের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য এটি অন্যতম উপকরণ, যা সেবার মান নিশ্চিতেও কাজ করে।
স্বাস্থ্যসেবার জন্য অ্যাক্রেডিটেশন গুরুত্বপূর্ণ হলেও দেশে আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানই এর জন্য আগ্রহী হয় না। কেননা এতে অনেক খরচ করতে হয়। দেশের নামিদামি বেসরকারি একটি হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, তার প্রতিষ্ঠান জেসিআইতে আবেদন করতে চেয়েছিল। তবে তারা অনেক বেশি ফি চাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। অ্যাক্রেডিটেশন মূলত একটি বাণিজ্যিক পণ্য। সাধারণত জেসিআইয়ের মতো সংস্থার প্রি-অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য ৪০ লাখ টাকা ফি দিতে হয়। এরপর তারা ট্রেনিং দেয়, ডকুমেন্টেশন করে। পরে একটি মক অডিট হয়। এতেও অনেক ফি দিতে হয়। এরপর মূল অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য ৫০ হাজার ডলার দিতে হয়। তিন বছর অন্তর দিতে হয় আরো ৫০ হাজার ডলার করে। তবে অ্যাক্রেডিটেশন না থাকলে বিদেশী রোগীরা চিকিৎসাসেবা নিতে আগ্রহী হন না। কেননা চিকিৎসার পর বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোর কাগজপত্র তাদের দেশের স্বাস্থ্যবীমা প্রতিষ্ঠানগুলো আমলে নিতে চায় না। এতে তাদের বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়।
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে সরকারির তুলনায় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার পরিসর বড়। সারা দেশে সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ৬৪০ (ইউনিয়ন পর্যায় বাদে)। আর অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে ৫ হাজার ৩০টি, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ১০ হাজারের বেশি এবং ব্লাড ব্যাংক ১৯২টি।
দেশে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কেবল ১০টির মতো বেসরকারি হাসপাতাল ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অ্যাক্রেডিটেশন রয়েছে। এ তথ্য জানিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক তিন কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, ‘প্রায় দেড় দশক আগে অ্যাক্রেডিটেশনের ওপর সরকার গুরুত্ব দেয়। বিষয়টি নিয়ে মূলত কাজ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল পরিচালক। তবে যারাই দায়িত্বে ছিলেন তারা এটিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। আবার কোনো বেসরকারি হাসপাতাল বা রোগ নির্ণয় প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনতে গেলে কিছু রাজনৈতিক চাপও থাকে। এক হাসপাতাল গ্রেড ‘এ’ আর অন্য হাসপাতাল গ্রেড ‘সি’ করলে চাপে পড়তে হয়।’
ওই কর্মকর্তারা আরো জানান, হাসপাতাল বা রোগ নির্ণয় প্রতিষ্ঠানের মান নিশ্চিতের দিক দিয়ে অন্তত ৫০০টি শর্ত ও নির্দেশনা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) অনেক নির্দেশনা আছে। জেসিআইয়ের অ্যাক্রেডিটেশনের বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী হাসপাতালগুলোকে তারকা চিহ্নিত করতে হয়। এতে ব্যয়ও অনেক বেশি। দেশে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অবকাঠামো নেই, লোকবল নেই। একই সঙ্গে অ্যাক্রেডিটেশনের আবহ তৈরি হয়নি।
রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) সাবেক পরিচালক ডা. আবু মোহাম্মদ জাকির হোসেন বণিক বার্তাকে বলেন, ‘সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই আস্থার সংকট রয়েছে। এক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন প্রয়োজন। এর মূল লক্ষ্য হলো চিকিৎসাসেবার সব মান নিশ্চিত করা। প্রতিটি পরীক্ষা, হাসপাতাল বা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের অবকাঠামো, জনবলের দক্ষতা থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয় নিখুঁতভাবে দেখা হয়।’
দেশের প্রথম সারির কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের জেসিআই, সিএপি, এনএবিএইচের অ্যাক্রেডিটেশন রয়েছে। এর মধ্যে ল্যাবএইড হাসপাতাল কয়েক বছর আগে এনএবিএইচ ও সিএপির অ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করেছে। এ বিষয়ে ল্যাবএইড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এএম শামীম বণিক বার্তাকে বলেন, ‘ভারতের এনএবিএইচ ও যুক্তরাষ্ট্রের সিএপির অ্যাক্রেডিটেশন আমাদের হাসপাতালের রয়েছে। এর মধ্যে প্যাথলজির জন্য রয়েছে সিএপি ও হাসপাতালের জন্য এনএবিএইচ অ্যাক্রেডিটেশন। হাসপাতালকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এ স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ। এটা না থাকলে বিদেশীরা বাংলাদেশে চিকিৎসা নিতে আগ্রহী হন না। ভারতে এমন নিয়ম আছে যে হাসপাতাল চালুর পর অ্যাক্রেডিটেশন নিতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক। তারা দুই বছর পরপর অ্যাক্রেডিটেশন নবায়ন করে।’
জেসিআইয়ের অ্যাক্রেডিটেশন রয়েছে এভারকেয়ার হাসপাতালেরও। এ বিষয়ে হাসপাতালটির বাংলাদেশ পরিচালক (মেডিকেল সার্ভিসেস) ডা. আরিফ মাহমুদ বণিক বার্তাকে বলেন, ‘আমাদের হাসপাতাল যখন প্রতিষ্ঠা পায় তখনই প্রচেষ্টা ছিল যেন আন্তর্জাতিক মানের সেবা দেয়া যায়। ২০০৮ সালে আমরা জেসিআইয়ের অ্যাক্রেডিটেশন লাভ করি। এ পর্যন্ত ছয়বার অডিট হয়েছে। দেশ থেকে বহু মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নিতে যান। তারা ভালো মানের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে চান। অ্যাক্রেডিটেশন সে মানের নিশ্চয়তা দেয়। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জেসিআই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সংস্থা।’
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২২ সালে ‘হেলথ কেয়ার অ্যাক্রেডিটেশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কেয়ার’ শিরোনামে এক প্রকাশনায় উল্লেখ করে, অ্যাক্রেডিটেশন বা স্বীকৃতি মূলত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা ও মান পর্যালোচনা করে। এ মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রমাণভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা, যথাযোগ্য সেবা, মানের স্তর, ক্লিনিক্যাল ও সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো পর্যালোচনা করা হয়।
অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য যেসব বিষয় মানা প্রয়োজন তা দেশের বেশির ভাগ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নেই বলে মন্তব্য করেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন ও রেফারেল সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শাহেদ আলী জিন্নাহ। তার মতে, দেশের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা নিয়ে মানুষের সন্তুষ্টি কম। আর অ্যাক্রেডিটেশন পেতে হলে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে হবে। এতে ব্যয়ও করতে হয় প্রচুর।
সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, ‘অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আইন হয়েছে। এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। হাসপাতালগুলোর যেন অ্যাক্রেডিটেশন থাকে তার জন্য সরকার কাজ করছে।’